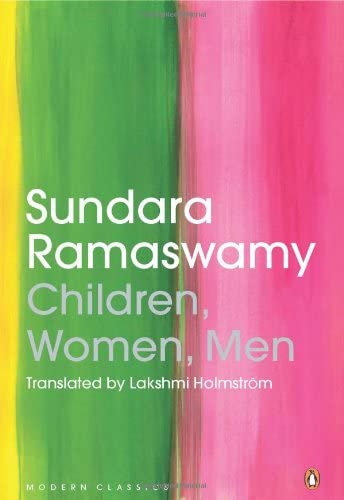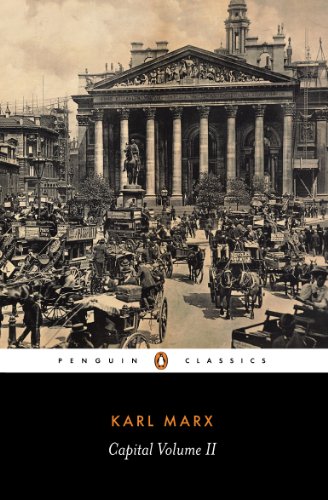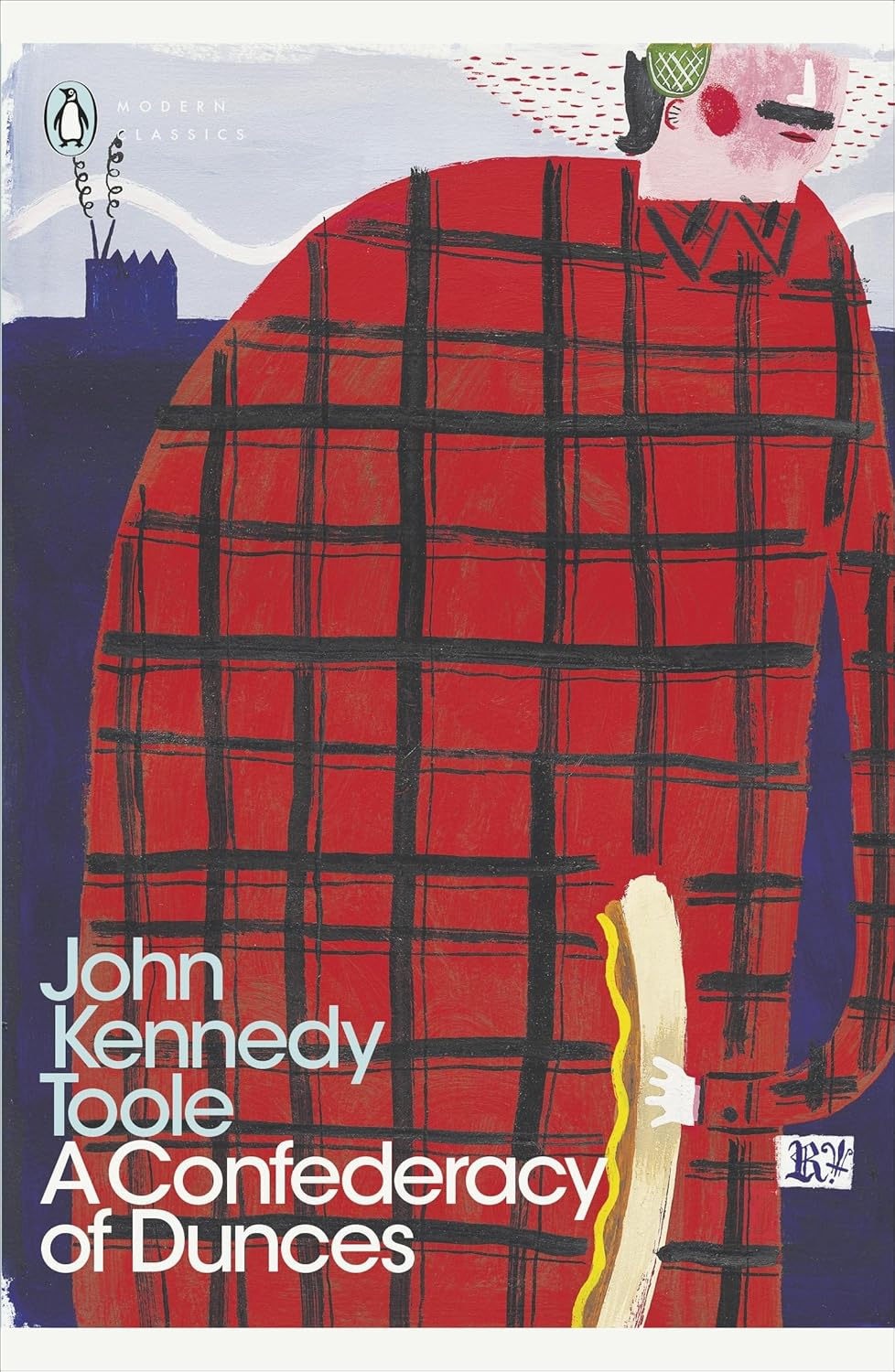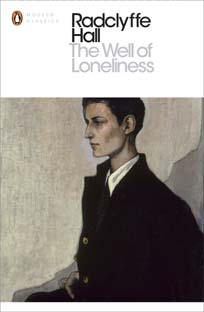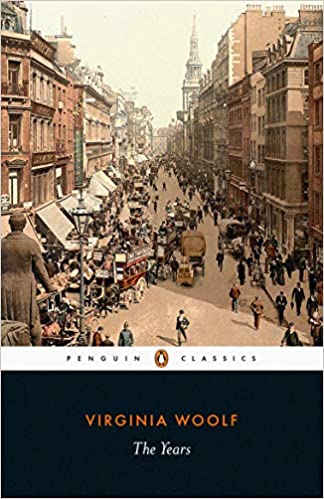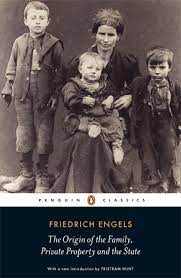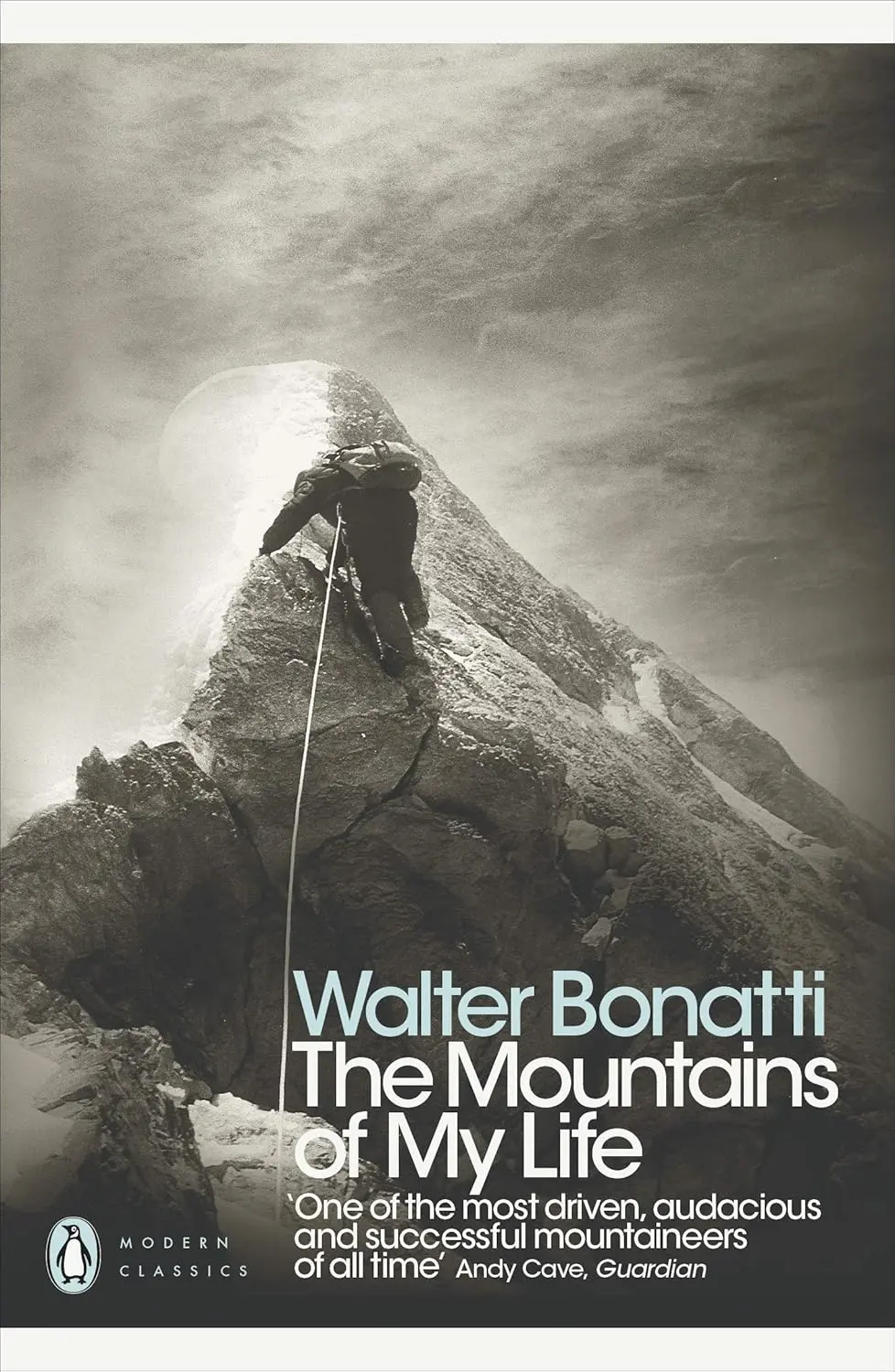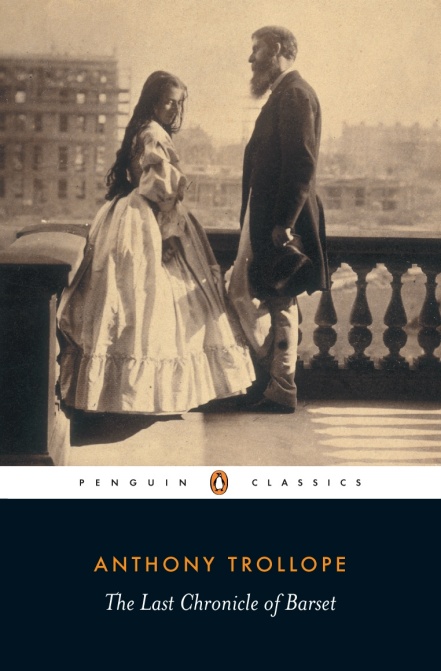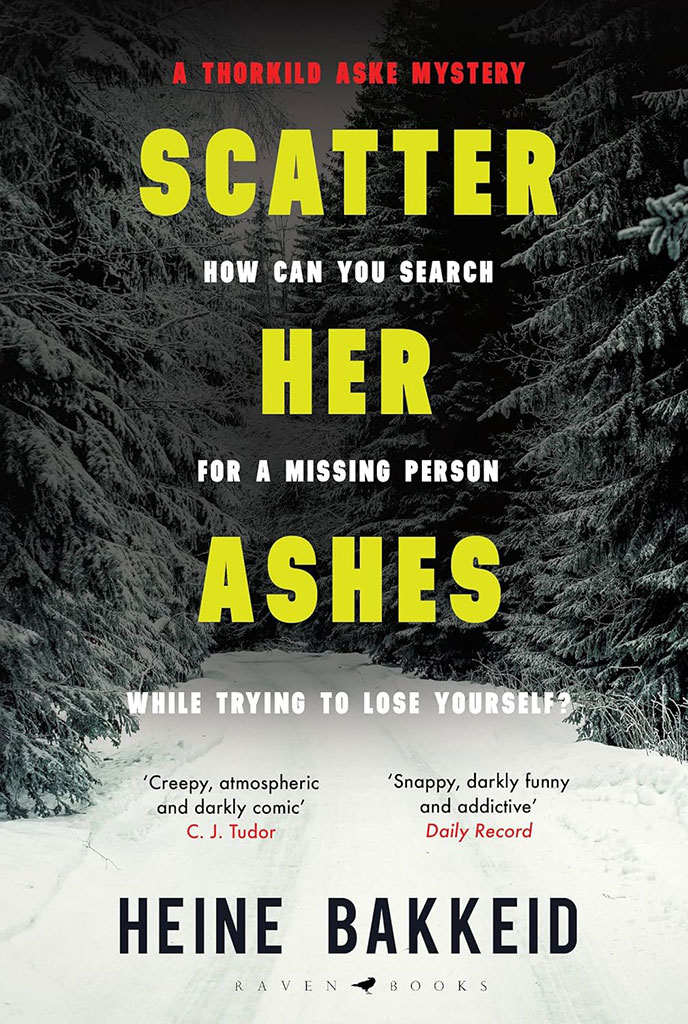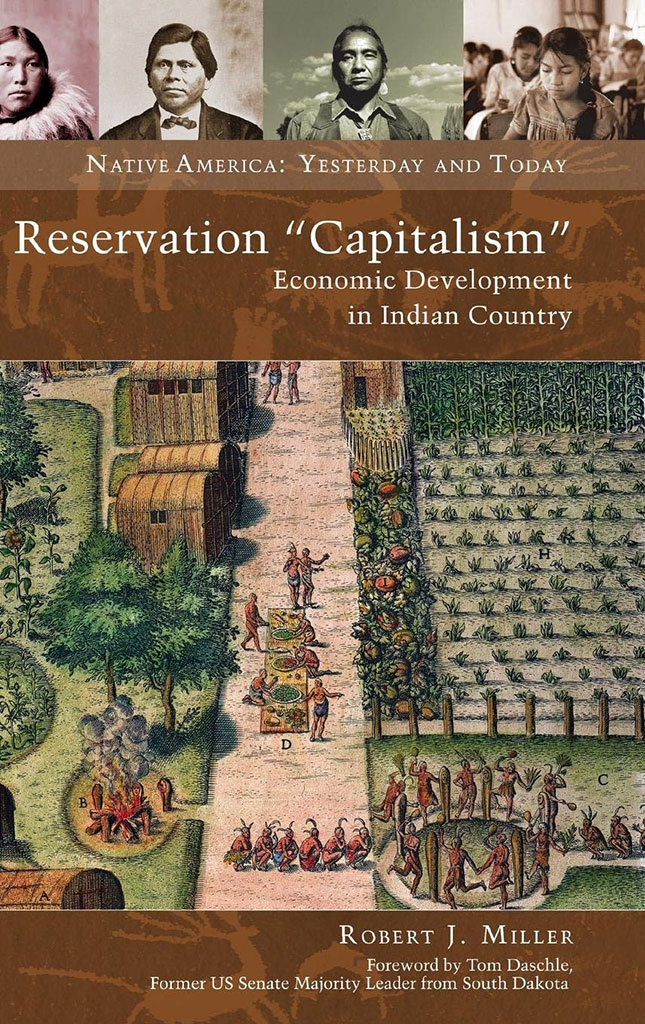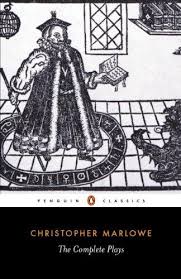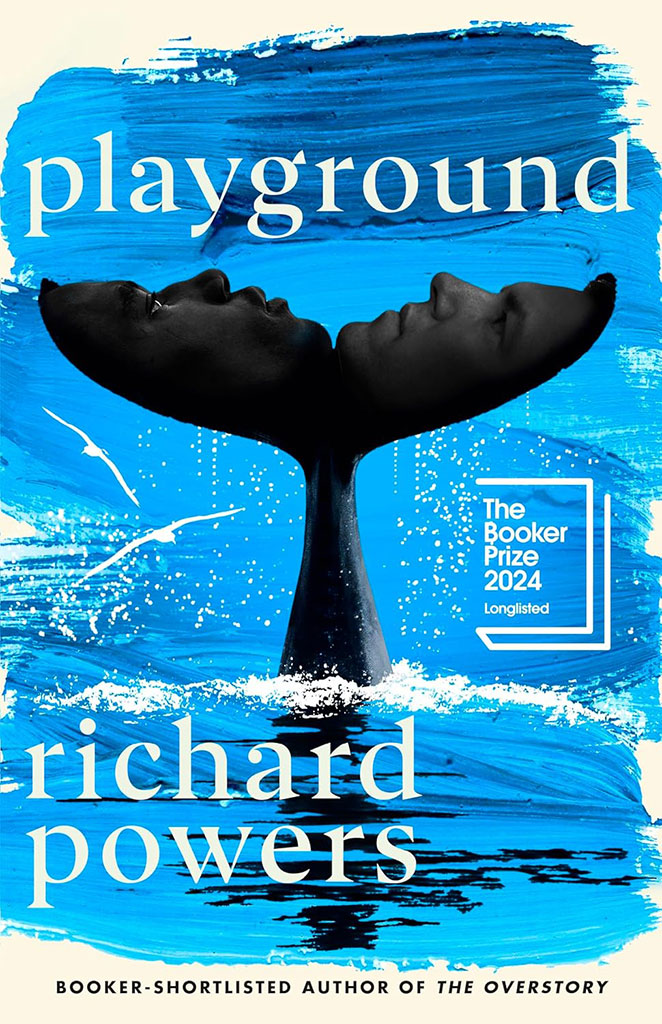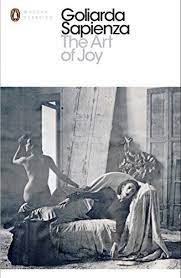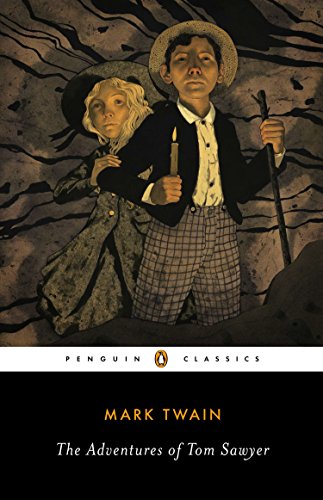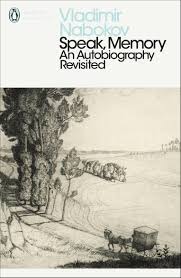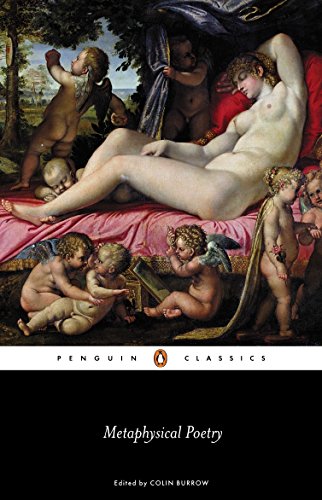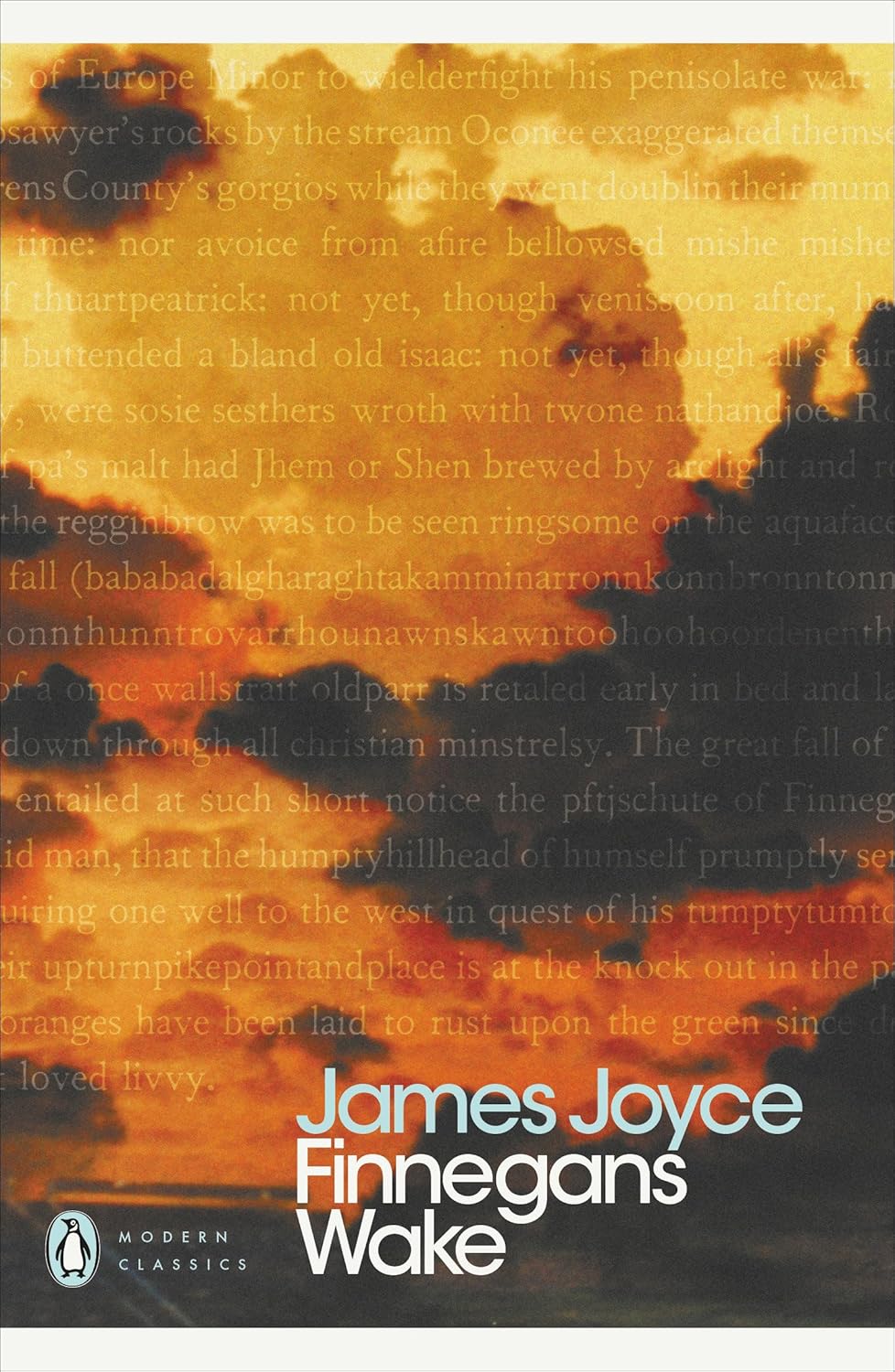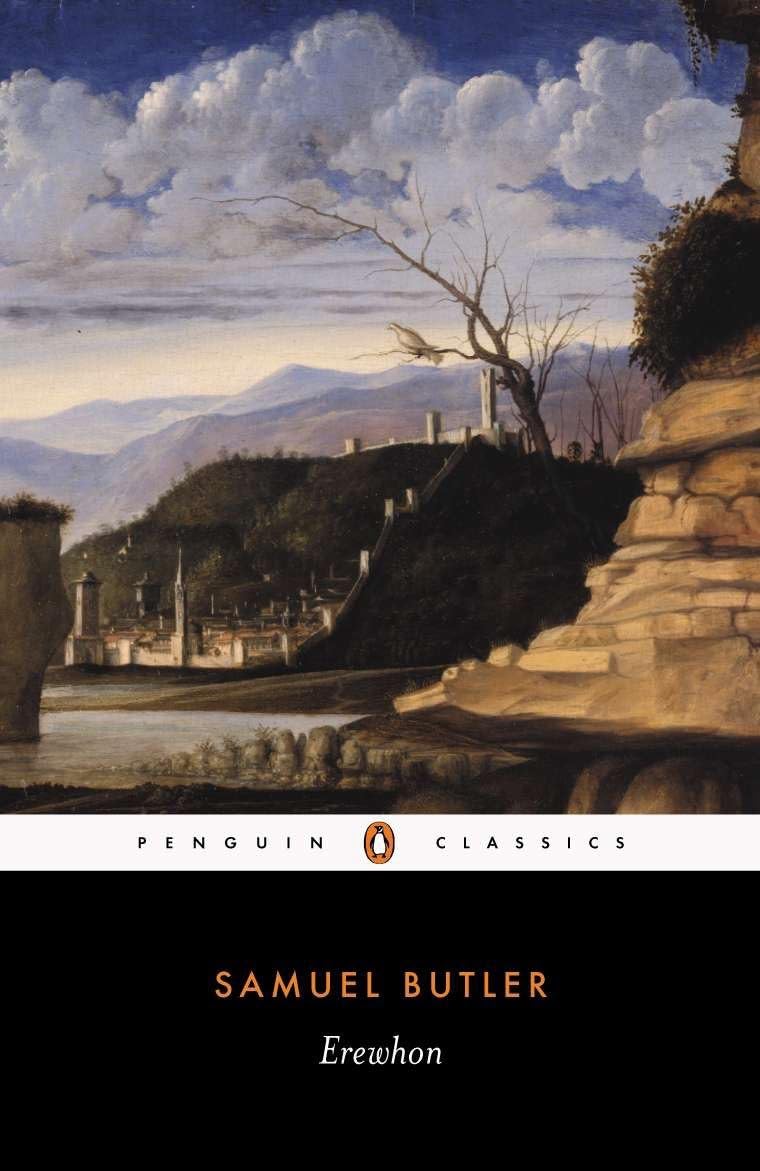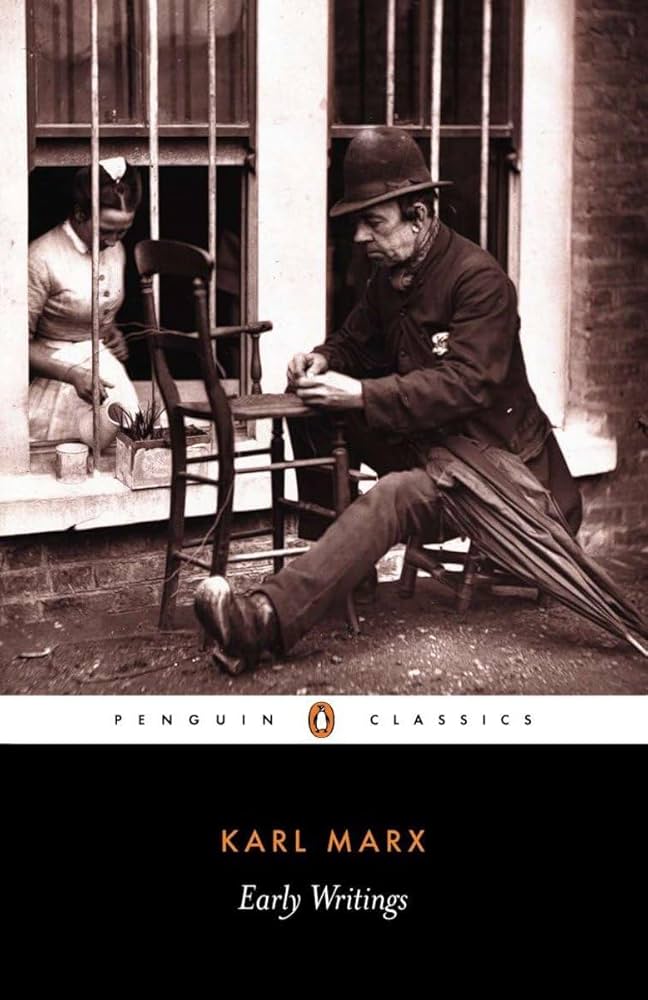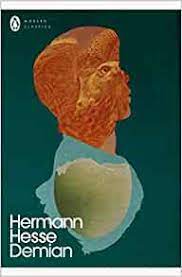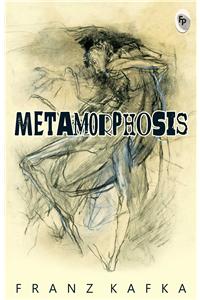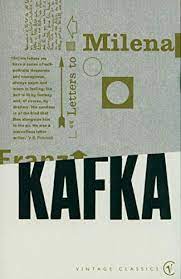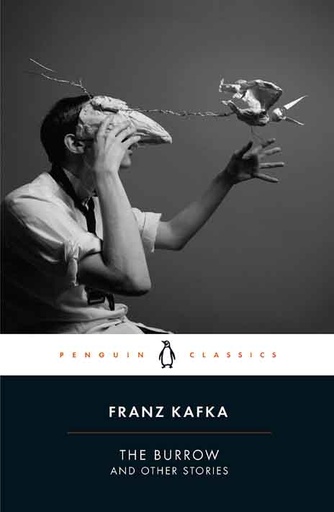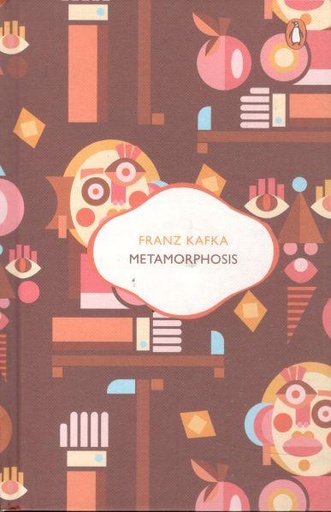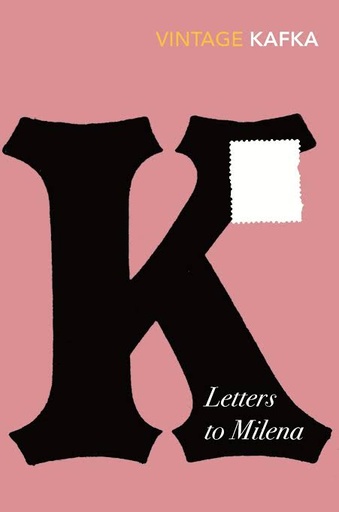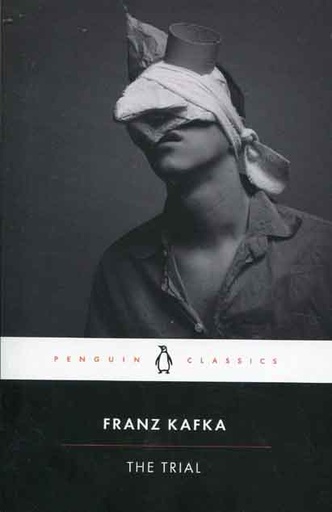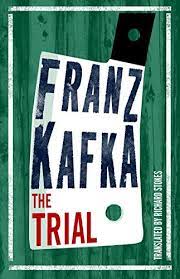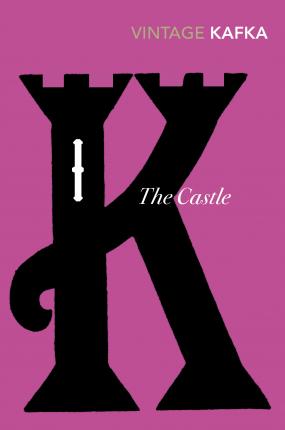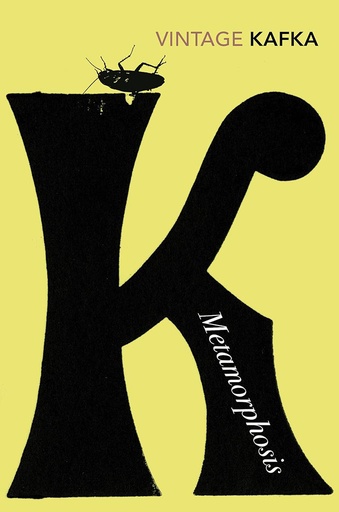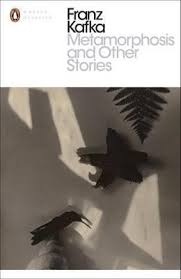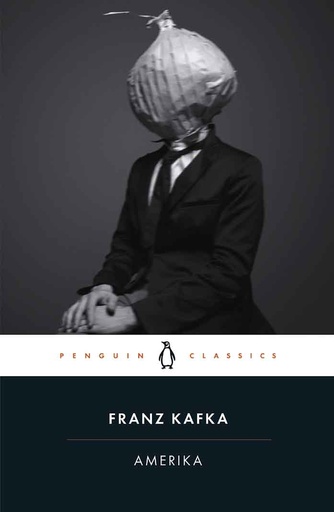অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, “য়ুরােপীয় দর্শনের ইতিহাস যেভাবে রচিত হয় সেভাবে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে য়ুরােপে একের পর এক দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং দর্শন প্রসঙ্গে তাঁর স্বাধীন চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এখানে- ভারতবর্ষে- এমন এক যুগে প্রধান সম্প্রদায়গুলির সূত্রপাত যার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য যৎসামান্যই এবং ঠিক কখন ও কিসের প্রভাবে ওই সুদূর অতীতে এক বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল সে-বিষয়ে কোন কথাই সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ-মন্তব্য অনুসরণ করেই ভারতীয় দর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দর্শনের ইতিহাস প্রায় একান্তভাবেই সম্প্রদায়গত।
কেননা, কোন এক সুদূর অতীতে কয়েকটি মূল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবার পর পরবর্তীকালের দার্শনিকতা বলতে প্রধানত সেগুলিরই বিকাশ। অর্থাৎ আমাদের দেশে যুগের পর যুগে একের পর এক নতুন ও স্বাধীন দার্শনিক মতবাদের আবির্ভাব হয়নি; তার বদলে দেখা যায় একই সঙ্গে বা পাশাপাশি কয়েকটি মূল মতের বিকাশ ঘটে চলেছে। একের পর এক দার্শনিক অবশ্যই এসেছেন; কিন্তু তারা অন্তত সচেতন ভাবে কোন নিজস্ব নতুন মত প্রস্তাব করতে সম্মত নন। প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি; অতএব হয়তাে নতুন করে পুরানাে কথাগুলিরই সমর্থন করেছেন। তাই চিন্তার মূল কাঠামােগুলি একই থেকেছে; দাসগুপ্ত যেমন বলেছেন, the types remained the same.
ভারতীয় দর্শনের সমর্থনে দাবি করা হয়েছে, দার্শনিক বিকাশের এ-বৈশিষ্ট্য মূল মতবাদগুলিকে ক্রমশই সুসম্বন্ধ ও সুউন্নত করেছে; অতএব মতবৈচিত্র্যের দিক থেকে ভারতীয় দর্শন যা হারিয়েছে দার্শনিক দৃষ্টির গভীরতা অর্জন করে তার কোন এক রকম ক্ষতিপূরণও করেছে। এই দাবির মূলে প্রকৃত সত্য যাই থাকুক না কেন, সেইসঙ্গেই একথাও স্বীকার্য, দার্শনিক বিকাশের এ-বৈশিষ্ট্য মতাদর্শগত এক সুস্পষ্ট নিশ্চলতারও পরিচায়ক। নতুন যুগের চিন্তাশীলের কাছেও প্রাচীন কালের চিন্তাই এক অদ্ভুত অলঙ্নীয়তা বহন করে এনেছে। “নতুন ব্যাখ্যাকারেরাও পূর্বগামী আচার্যদের ব্যাখ্যায় নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন এবং কখনই তার বিরােধিতা করেননি।”
সুদীর্ঘকাল ধরে একই সম্প্রদায়ের আচার্য-পরম্পরার মধ্যে ধ্যানধারণার কোন পরিবর্তনই ঘটেনি- এ কথা অবশ্যই ঠিক নয়। কিন্তু এই পরিবর্তনেও কোন এক বৃহত্তর অপরিবর্তনীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেন সেই অপরিবর্তনীয়তা? সাধারণভাবে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের মূল অপরিবর্তনীয়তার মধ্যে হয়তাে তার মূলসূত্র অন্বেষণ করা যায়। “আপাতদৃষ্টিতে ভারতের অতীত যতই পরিবর্তনশীল বলে প্রতীত হােক না কেন, সুদূরতম কাল থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে।” ‘রাষ্ট্রনৈতিক আকাশের ঝােড়াে মেঘ সমাজের অর্থনৈতিক উপাদানের কাঠামােকে বদলাতে পারেনি।
এ-জাতীয় পরিস্থিতি চিন্তাজগতে নিত্য-নতুন অভিযানের পক্ষে প্রশস্ত নয়; বিশ্বরহস্য ও মানব-সমস্যা নিয়ে নিত্য-নতুন সমাধান খোজবার প্রেরণা এআবহাওয়ায় স্বাভাবিক নয়। কেননা বাস্তব অবস্থা হলাে, দীর্ঘকাল ধরে জীবনধারণের অবস্থা একই থেকেছে; অপরিবর্তিত থেকেছে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী আর মানুষের ভাগ্য। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বাঁধা থেকেছে প্রত্যেকের জীবনধারণ পদ্ধতি আর কর্মফলবাদ মানুষকে শিখিয়েছে এই নিশ্চল ভাগ্য নিয়ে অভিযােগ নিষ্ফল। বেকন বলেছিলেন, “মানুষের শক্তি এবং মানুষের জ্ঞান উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক প্রায় তাদাত্ম-বর্তমান।” “অতএব মানুষের চিন্তাবিকাশ আর ভাগ্যবিকাশ আসলে একই কথা।” ভারতে কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উৎপাদন কৌশলের মৌলিক উন্নতি বা পরিবর্তন সাধিত হয়নি; আর তাই উন্মােচিত হয়নি পৃথিবীকে জয় করবার- অতএব বােঝবারও-নিত্যনতুন সম্ভাবনা।
আমাদের দেশের দার্শনিক সাহিত্যের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের ফলেই দেখা যায় কুম্ভকার ও তন্তুবায় আর তাদের ঘট আর পট- কীভাবে দার্শনিক চিন্তাদিগন্তের সীমারেখা নির্দেশ করেছে : এ-জাতীয় সাবেকী কলাকৌশলকেই দার্শনিকেরা যেন অক্লান্তভাবে দার্শনিক অনুমানের দৃষ্টান্ত করেছেন। এ-পরিস্থিতিতে দার্শনিক প্রচেষ্টা অভিনব তত্ত্বে উপনীত হবার পরিবর্তে মােটের উপর প্রাচীন তত্ত্বের কাঠামাের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উত্তরকালের দার্শনিকদের কাছেও সেই প্রাচীন তত্ত্বগুলিই অভ্রান্ত ও অমােঘ। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে ভারতীয় ইতিহাসে অসামান্য দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি-দার্শনিকের পরিচয় পাওয়া যায় না। নাগার্জুন, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি, উদ্দ্যোতকর, উদয়ন, কুমারিল, বাচস্পতি মিশ্র প্রায় এলােমেলােভাবেই আরাে অনেক নাম করা যায়- দার্শনিক প্রতিভার বিচারে যে-কোন দেশের ইতিহাসেই যারা দিকপাল বিবেচিত হবেন।
কিন্তু তারা নিজেরা দার্শনিক হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র দাবি করবেন না, দেশের ঐতিহ্যও তাঁদের এ-স্বাতন্ত্র দিতে প্রস্তুত নয়। প্রত্যেকেই কোন এক প্রাচীন সম্প্রদায়ের সমর্থক। এবং এই সমর্থন-প্রসঙ্গে যখন কোন দার্শনিক স্পষ্টতই কোন অভিনব তত্ত্বর অবতারণা করেন তখনাে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন যে, যে-প্রাচীন জ্ঞানের তিনি প্রতিনিধি তারই মধ্যে এ-তত্ত্ব বীজাকারে বর্তমান ছিল। সম্প্রদায়গুলির মূল গ্রন্থ বলতে সাধারণত এক-একটি সূত্রসংকলন। সংকলিত সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রায়ই পূর্ণাঙ্গ বাক্যও নয়। পরবর্তীকালে দার্শনিক সাহিত্য বলতে প্রধানতই সূত্রগুলির ভাষ্য এবং সেই ভাষ্যর উপর টীকা-টিপ্পনী। তাছাড়াও অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যায় কিছু কিছু স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হয়েছে। যেমন পদ্যে লেখা ‘কারিকা এবং বার্তিক, এবং গদ্যে লেখা নানা গ্রন্থও। কিন্তু সাধারণত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছেই সূত্রগ্রন্থগুলিই চরম জ্ঞানের আকর বলে বিবেচিত।
Delivery Charge (Based on Location & Book Weight)
Inside Dhaka City: Starts from Tk. 70 (Based on book weight)
Outside Dhaka (Anywhere in Bangladesh): Starts from Tk. 150 (Weight-wise calculation applies)
International Delivery: Charges vary by country and book weight - will be informed after order confirmation.
3 Days Happy Return. Change of mind is not applicable
Multiple Payment Methods: Credit/Debit Card, bKash, Rocket, Nagad, and Cash on Delivery also available.


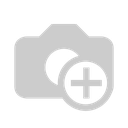
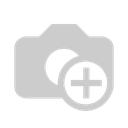
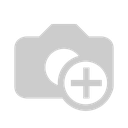
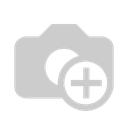
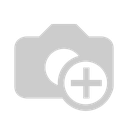
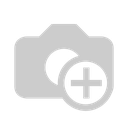
?unique=9366d88)